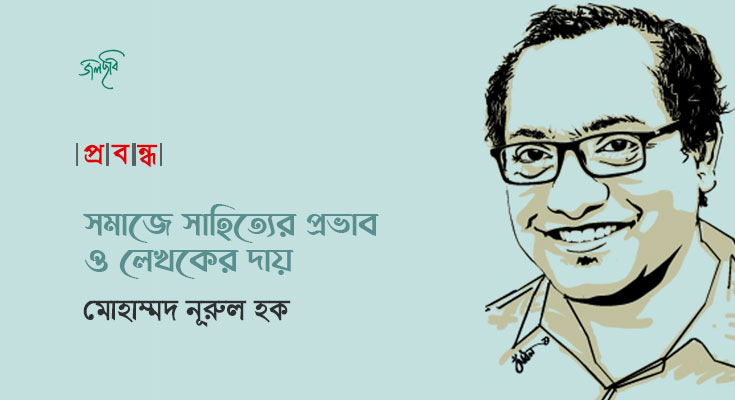লেখালেখি করে কী হয়?—এমন একটি প্রশ্ন বেশকিছু দিন ধরে সাধারণ মানুষ তো বটেই খোদ লেখকদের কাছ থেকেও উঠছে। লেখালেখি করে কী হয়—এই প্রশ্নের দুটি দিক রয়েছে। একটির উদ্দেশ্য সমাজের ওপর সাহিত্যের প্রভাব কী, তা জানার; অন্যটি সাহিত্যচর্চাকার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ। জানার ইচ্ছায় হোক আর বিদ্রূপের উদ্দেশ্যেই হোক—প্রশ্ন উঠছে যখন, তখন এর জবাবও খুঁজতে হবে। জবাব খুঁজতে গেলে প্রয়োজন হবে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের। আর এই কার্যকারণ সম্পর্কের পেছনে রয়েছে লাভ-ক্ষতির হিসাব।
আবার লাভ-ক্ষতির হিসাব কষার নেপথ্যে কাজ করছে কল্যাণ-অকল্যাণচিন্তা। অর্থাৎ একটি প্রশ্ন যখন উঠছে, তখন তার পেছনে একটি উত্তরও নিশ্চয় রয়েছে। সেই উত্তরের পেছনে পেঁয়াজের খোসার মতো একের পর প্রশ্নের আবরণও থাকবে। এবার সে-সব প্রশ্ন, প্রশ্নের নেপথ্য কারণ ও সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে দেখাই সাহিত্যিকর্মীর কাজ।
যারা বলছেন, ‘লেখালেখি করে কী হয়’—আগে তাদের শ্রেণী-বয়স-পেশা শনাক্ত করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, কারা এই ধরনের প্রশ্ন তুলছেন? তারা সমাজ থেকে প্রত্যাশা করছেন? আবার যারা সমাজ থেকে ‘কিছু পাওয়ার’ প্রত্যাশা করছেন, তারা সমাজকে কী দিয়েছেন, সেটিও বিবেচনায় আনতে হবে।
সাধারণত লাভ-ক্ষতির হিসাব করে বণিকসম্প্রদায়। যারা অর্থ বিনিয়োগ করে লাভালাভের হিসাব করে। একজন ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, আড়ৎদার কিংবা শিল্পপতি বিভিন্ন খাতে ভিন্ন-ভিন্ন মেয়াদে অর্থ বিনিয়োগ করেন। মেয়াদ শেষে বিনিয়োগ তুলে আনার পাশাপাশি মুনাফাও আশা করেন। সম্প্রতি কিছু কিছু কৃষকও বাণিজ্যিকভিত্তিতে চাষাবাদ করছেন। ফসল চাষ থেকে লাভের আশা করছেন তাঁরা। যে ফসল চাষে তাঁরা লাভের মুখ দেখেন না, সেই ফসল পরের বার চাষ থেকে বাদ দিয়ে বিকল্প ফসলে মনোযোগ দেন। মৌসুম শেষে যে ফসলে লাভের মুখ দেখেন, চাষি সেই ফসল চাষে মনোযোগও বেশি দেন। এই লাভ মূলত বৈষয়িক-অর্থনৈতিক। অর্থাৎ যেখানে অর্থ বিনিয়োগ করলে লাভের সম্ভাবনা বেশি, বিনিয়োগকারীর আগ্রহও সেখানেই। এটি মানবস্বভাবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।
কিন্তু সমাজচিন্তক, শিল্পী, সাহিত্যিকের এমন নগদ-অর্থপ্রাপ্তির চিন্তা শোভনসম্মত নয়। সাহিত্যিককে মনে রাখতে হবে, তার কাজ আর সমাজকর্মী কিংবা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর কাজ এক নয়। সমাজকর্মী ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর কাজ দৃশ্যমান। সেই কাজের ফলভোগীরা সমাজের দশজন। কারণ, প্রকৃত কবিতা সমাজ-রাষ্ট্র-মানুষকে উপেক্ষা করে রচিত হয় না। মানবকল্যাণের উদ্দেশ্য যে কবিতায় উপেক্ষিত, সে কবিতা সাময়িক মনোরঞ্জনের উপচার হয় মাত্র; চিরকালের মন জাগাতে পারে না। মন জোগাতে পারলেই সে কবিতার উদ্দেশ্য শেষ, চিরকালের পাঠ্য হওয়ার কোনো গূঢ়ার্থ সেখানে থাকে না। কবি সামাজিক, তাই সমাজের ভালো-মন্দে তাঁর ভেতরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রাত্যহিক ঘটনাবলিও তাঁর চিন্তার বিষয়।
সাহিত্যের প্রভাব সমাজে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে না। রাজনৈতিক নেতাকর্মী-সমাজকর্মীর কাজ ছোট নদীর ঢেউয়ের মতো। দূর থেকেও তা দৃশ্যমান। কিন্তু সাহিত্যিকের কাজ মহাসমুদ্রের মধ্যভাগের তলদেশের জলরাশির মতো। অতিকায় জাহাজ চলাচলেও যেখানে ঢেউ দৃশ্যমান হয় না। তাঁর কাজ অতল গভীরে, নিঃশব্দের বয়ে চলা স্রোতের মতো। সাহিত্যিককে মনে রাখতে হয়, কেবল কল্পনা ও অভিজ্ঞতার সুষম বিন্যাসেই সাহিত্যকর্ম সম্পন্ন হয় না। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হয় সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম-দর্শনের অনুষঙ্গও। সামাজিক দায় অনুভবের ছাপ রাখতে হয় সৃষ্টিতে। ব্যক্তিকে হয়ে উঠতে হয় সমষ্টির প্রতিনিধি। যিনি সমষ্টির প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেন, তাঁর সৃষ্টি জনগণের সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। একবার যে সৃষ্টি জনগণের সম্পদে পরিণত হয়, তা সাধারণত কয়েকযুগেও বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবে যায় না। এই কথা সহজেই অনুমান করা যায়, বাল্মিকীর রামায়ণ এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মহাভারত তাঁদের স্ব-স্ব কালের সমাজ পরিবর্তনে বিপুল ভূমিকা পালন করেছে।
বিশেষত, ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ জাগ্রত করতে এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও অধর্মের বিনাশে এই দুটি মহাকাব্য দুই রচয়িতা মহাকবির জীবদ্দশায় সমাজ পরিবর্তন ও বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাই দুই কবির প্রয়াণের কয়েক হাজার বছর পরও লোকে তাঁদের ঋষিতুল্য সম্মান করে। একইসঙ্গে কালের বিবর্তনে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি ধর্মীয় গ্রন্থরূপেও সমাজে সমাদৃত হচ্ছে। বাংলা ভাষার দিকে তাকালেও অনুরূপ সাহিত্যকর্মের দৃষ্টান্ত মিলবে। বিশেষত, রাজা রামমোহন রায়ের ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সম্বাদ পুস্তিকা’ (১৮১৮) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৫) পুস্তিকাসহ এমন বহু গ্রন্থ র চনা করে গেছেন, যেগুলো শতবর্ষ পরেও হিন্দু নারীদের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে আছে। সাহিত্যের শক্তি এখানেই। মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদ-সিন্ধু’। প্রথম দুজনের সাহিত্যকর্ম হিন্দু সমাজের বিপুল পরিবর্তন এনেছে, শেষোক্তজনের সাহিত্যকর্ম মুসলিম সমাজের বিশ্বাসকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে। ‘বিষাদ-সিন্ধু’ পাঠে বাঙালি মুসলমান সমাজ ইতিহাসের সত্য থেকে দূরে সরে আসতে প্ররোচিত হয়েছে। বিষাদ-সিন্ধুর পাঠক বাঙালি মুসলমানের কাছে হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর নাতি ঈমাম হাসান ও ঈমাম হোসেন নির্দোষ মুসলমান, আর এজিদ কাফের হিসেবেই পরিগণিত। অথচ ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন, এজিদ হলেন হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় সাহাবি হজরত মুয়াবিয়ার সন্তান। অর্থাৎ ঈমাম হাসান-ঈমাম হোসেনের মতোই এজিদও মুসলমান। কিন্তু মীর-মানসে এজিদ হয়ে গেলেন কাফের। আর তাঁর পাঠককূলও সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলেন। কালের যাত্রায় আজও সেই বিশ্বাস থেকে মানুষের মনে অনড় হয়ে আছে।
সাহিত্যিককে লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে হয় না। তার ধর্ম—কর্ম করে যাওয়া। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, ‘হে অর্জুন কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না।’ অর্থাৎ রণভূমিতে বীরের ধর্ম হলো যুদ্ধ করে যাওয়া। তার ফল কী হবে, তা নিয়ে চিন্তিত হওয়া বীরের ধর্ম নয়। ফল পূর্ব-নির্ধারিত। যুদ্ধে জয়লাভ করলে কাঙ্ক্ষিত রাজ্য কিংবা রাজত্ব কিংবা সিংহাসন অথবা অন্য যে-কোনো বস্তু লাভ হবে। আর হেরে গেলে মৃত্যু কিংবা দাসত্বের শৃঙ্খল পরতে হবে। অর্জুনের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছেন, তা আজকের সাহিত্যিকদের জন্যও পালনীয়। তাঁদের দায়িত্ব হলো—কর্ম করে যাওয়া। সেই কর্ম সমাজের কল্যাণের স্বার্থে, মঙ্গলের স্বার্থে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছেন, ‘বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।’১ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে মানবসৃষ্ট কর্ম বলে স্বীকার করেও তাকে দ্বৈববাণী বলে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই—মানুষ যখন বিশ্বলোকের কল্যাণের চিন্তা করে, তখন তা আর ব্যক্তিবিশেষের চিন্তামাত্র থাকে না। তাহয়ে ওঠে সমষ্টির চিন্তা। আর সমষ্টির চিন্তা যিনি করেন, তিনি একক কোনো ব্যক্তিহৃদয়ের দাবিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না। তিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণচিন্তায় নিজেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত সত্তা মনে করেন। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মও তখন আর ওই লেখকের নিজস্ব সম্পদে সীমাবদ্ধ থাকে না। একইসঙ্গে তাকে আর নিছকই মানবের বাণী বলেও তুচ্ছ করা যায় না। তা মানবমনের কথা হয়ে দ্বৈববাণীর মর্যাদায় উন্নীত হয়।
জগৎ-সংসারে যারা বিশ্বাসী, বিশেষত ঐশীধর্মে যাদের গভীর-গভীরতর আস্থা রয়েছে—তাঁরা দ্বৈববাণীতেই আস্থা রাখেন সন্দেহাতীতভাবে। তাঁদের সেই আস্থায় কোনো জড়পদার্থ কিংবা বিজ্ঞানের প্রমাণিত শক্তিও অনেক সময় চিড় ধরাতে পারে না। কারণ তারা বস্তুসত্যের প্রমাণ চান না, চিত্তে অনাবিল শান্তি কামনা করেন। ফলে তাঁদের কাছে যুক্তি ও বিজ্ঞানের চেয়ে চিত্তে শান্তিদায়ী অমিয়বাণীই বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সম্ভবত এ কারণে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকর্মকে ঐশীবাণী বলে উল্লেখ করেছেন। ফলে ঐশীবাণীতে আস্থাবানরা যেমন ঐশীবাণী অনুযায়ী নিজ-নিজ কর্মপন্থা তৈরি করতো, তেমনি সাহিত্যে অনুপ্রাণিতরাও সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে।
সাহিত্য সমাজকে যা দেয়, তা সাদা চোখে দেখা যায় না। তার জন্য দর্শককে পূর্বাপর ঘটনার পরম্পরা বিচার করতে জানতে হয়। যে সময়কালে দাঁড়িয়ে প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছেন, সেই সময়ে একযুগ আগে তাঁর সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, ওই সময়ের সাহিত্যিকর্মে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার কতটা প্রকাশিত হয়েছিল, তার সঙ্গে উপস্থিতকালের পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, ‘সহমরণপ্রথা বিলোপ’, ‘বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন’, ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ’, ‘যৌতুকবিরোধী আন্দোলন’, ‘অ্যাসিডবিরোধী সমাজসচেতনমূলক আন্দোলন’ভিত্তিক প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্প-কবিতা-নাটক-সিনেমা-গানের কথা। সমাজ থেকে সহমরণ প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায়। তিনি একের পর এক প্রবন্ধ রচনা করে সহমরণ-প্রথা অ-শাস্ত্রীয় ও অমানবিক-নিষ্ঠুরতা তা প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমেই সহমরণবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সহমরণের মতো নিষ্ঠুর-অমানবিক প্রথা বিলুপ্তির জন্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি, সমাজপতি কিংবা ধর্মব্ত্তোরা এগিয়ে আসেননি। হিন্দু বিধবাদের জীবনদানে এগিয়ে এসেছিলেন একজন সাহিত্যিক।
হিন্দু বিধবাদের জীবনদানের কাজটি রাজা রামমোহন রায় করার পর তাদের পুনঃবিয়ের পথে এগিয়ে এসেছেন আরেক সাহিত্যিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
রাজা রামমোহন রায় নবজীবন দেওয়ার পর বিধবার জীবনকে নতুন করে রাঙিয়ে দেওয়ার আন্দোলনে ব্রতী হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শেষোক্তজনের কাজ অনেক কঠিন, দায়িত্বপূর্ণ সরাসরি প্রচলিত সমাজরীতি বিরুদ্ধে ছিল। তবু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন স্বীয় পরিকল্পনায়-সিদ্ধান্তে অনঢ়-অবিচল। তাঁর এই আন্দোলনের প্রভাব সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে যেমন পড়ে, তেমনি সাহিত্যজগতেও বিপুল আলোড়ন তোলে। তাঁর সমসাময়িকরা তো বটেই, পরবর্তীকালের সাহিত্যিকরাও বিধবাবিবাহ নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ছোটগল্প ও উপন্যাসে পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন।২
সমাজের এত বড় দুটি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে দুই মহান সাহিত্যিকের প্রাণপণ প্রচেষ্টার ফলে। সেখানে রাজনীতিবিদ, ধর্মবেত্তারা কোনো সহযোগিতা করেননি। পরন্তু তারা পাহাড়সমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—এই ইতিহাস আজ জ্বলন্ত সত্য।
এত বড় দুটি প্রমাণ উপস্থিত করার পরও যারা বলবেন, সাহিত্যচর্চা করে কী হয়—তাঁদের সামনে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে হবে—ভাত-মাছ-মাংস-সবজি ক্ষুধার্তের পেট করে। পানি তৃষ্ণা মেটায়। কিন্তু হাওয়া কি খেতে পারা যায়, না পান করা যায়? হাওয়া কি ধরা যায়, না ছোঁয়া যায়? তবু খাদ্য না খেয়েও মানুষ দিনের পর দিন বাঁচতে পারে, কিন্তু হাওয়াভিন্ন কয়েকমুহূর্তও বাঁচা সম্ভব নয়। হাওয়া দৃশ্যমান কোনো উপকারণ করে না সত্য, তার উপস্থিতিও জানান দেয় না, এও সত্য। প্রকৃত সত্য ভিন্ন। তাহলো—হাওয়ার অভাবে মানুষ তো বটেই, কোনো প্রাণী এমনকি জীবও বাঁচতে পারে না। তেমনি মানবজাতির আরও আরও কর্মের ভিড়ে সাহিত্যও দৃশ্যের আড়ালে থেকে নিরন্তর মানবকল্যাণের কাজটি করে যায়। যুগে-যুগে ভেতরে ভেতরে সাহিত্য সমাজের বিপুল পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। কখনো সেই ভূমিকা প্রচ্ছন্নভাবে, কখনো প্রকটভাবে। যিনি সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা অস্বীকার করবেন, তিনি হয়তো হাওয়া থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করেন বলে মানেন না। নয়তো জানেন না। তাই সাহিত্যের সামাজিক মূল্যও স্বীকার করেন না।
এই প্রসঙ্গে জীবেন্দু রায়ের উক্তি স্মরণ করা যাক। তিনি ‘সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, ‘… জীবনই সেখানে প্রকাশ পাবে তার প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সমেত, তবে কলা বা শিল্পের অনুশাসন মেনে তথা রসসৃষ্টিকেই প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করে।’৩ এটুকু বলেই তিনি থামেননি।
সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের নিয়ামকগুলো কার্যকরী ভূমিকা প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট করে জীবেন্দু রায় ওই প্রবন্ধে বলেছেন,
এটুকু অনুশাসন মেনে নিলে সমাজপরিবর্তনে বা জীবনের বাঞ্ছিত রূপের চিত্রায়ণে সাহিত্যের সদর্থক ভূমিকা থেকেই যায়। ‘সমাজ পরিবর্তন’ বলতে বিপ্লব বা আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির চেষ্টা বা প্রতিশ্রুতি নয়, মানুষের মনের নতুন কালের উপযোগী নির্মাণের উদ্যোগ-প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু সেই পরিবর্তনের দায়িত্ব জীবনের ধর্মেই গোচরে অথবা অগোচরে নেয়। বঙ্কিমের ‘বিষবৃক্ষ’ বা ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’- এর পর ‘নষ্টনীড়’ বা ‘চোখের বালি’-র সমাজ মন আর অতটা অনড় থাকেনি।৪
শতবর্ষ আগে সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা আজ প্রমাণিত। বিশেষত বাল্মিকী, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মীর মশাররফ হোসেনে সাহিত্যকর্মের প্রভাব সমাজকে কতভাবে প্রভাবিত করেছে, তা নিয়ে আজ আর নতুন করে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। অতীতে যদি সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্য ভূমিকা রাখতে পারে, বর্তমানেও পারবে। পারবে ভবিষ্যৎ-পৃথিবীর গতিপথ তৈরিতেও ভূমিকা রাখতে। এই প্রসঙ্গে ‘সমাজ ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে আবদুল হক বলেছেন, ‘এটা সুপ্রমাণিত যে, সাহিত্য কেবল পাঠককে আনন্দ দেয় না, তাঁকে প্রভাবিত করে, এবং সমাজকেও। কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্য সর্বদাই সমাজকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে এসেছে।’৫
এখানে আরেকটি বিষয় প্রাসঙ্গিক। একদা সমাজ পরিবর্তনে বিপুলভাবে ভূমিকা রাখতো ধর্ম। ধর্মপ্রবর্তকেরা সমাজ থেকে অধর্ম ও অন্যায়কে দূর করার জন্য যুগে যুগে নতুন নতুন বার্তা নিয়ে আসতেন। তাঁদের সেই বার্তা সমাজের ওপর বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করতো। বর্তমান সময়ে সেই ধর্মীয় অবতারের আভির্ভাব আর হয় না। ফলে নতুন ধর্মের প্রবর্তন হয় না। সমাজ-সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনে সেই ভূমিকা এখন পালন করেন সমাজচিন্তক ও সাহিত্যিকেরা। বিষয়টিকে পরিষ্কার করেছেন আবুল ফজল। ‘সমাজ ও সাহিত্য’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,
‘নবী আগমনের পথ বন্ধ গেছে চিরতরে, এখন নবীদের সামাজিক কর্তব্য এসে বর্তেছে শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর। তাই নবীদের মতো তাঁদেরও থাকতে হয় চির-সচেতন আর দায়িত্বশীল। এক হিসেবে নবীদের চেয়ে লেখকদের সামাজিক দায়িত্ব অনেকগুণ বেড়ে গেছে, কারণ নবীদের আমলে সমাজ ছিল গণ্ডিবদ্ধ, ঐ সমাজের কর্মকাণ্ড আর ক্রিয়াকলাপ ছিল নিতান্ত সীমিত।’৬
এতক্ষণে মনে হয় সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকার একটি পরিচয় পরিষ্কার হয়েছে। সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে একটি যে-সম্পর্ক, তা দৃশ্যমান নয়; সম্পূর্ণই আত্মিক। আত্মা যেমন বাইরে থেকে দেখা যায়, স্পর্শেরও অতীত, কেবল অনুভব করা যায়; সমাজের ওপর সাহিত্যের ভূমিকাও তেমন। সমাজকে সাহিত্য সূর্যের আগুন দিয়ে পোড়ায় না, কিন্তু তেজ ও আলো দিয়ে দীপ্তিমান করে তোলে। সূর্য যেমন দূর থেকে সৌরজগৎকে বাঁচিয়ে রাখে, বৃক্ষ যেমন মাটির গভীরে তার শেকড়ের মাধ্যমে সঞ্জিবনী সংগ্রহ করে, সাহিত্যও তেমনি সমাজকে গভীরে থেকেই প্রাণবায়ু দিয়ে যায়।
আর অর্থনৈতিক লাভা-লাভের বিষয়টিও একেবারেই তুচ্ছ নয়। যিনি সাহিত্যচর্চা করেন, তিনি আর্থিকভাবেও কিছুটা লাভবান তো হন। আর শিক্ষাঙ্গনে যিনি সাহিত্যের শিক্ষকতা করেন, তিনিও সাহিত্য পড়িয়েই জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। ফলে সাহিত্যচর্চার আর্থিক মূল্য নেই, কথাটা খাটে না। এদিক থেকে দেখলে ব্যবসায়ীদের মতো সাহিত্যসেবীদেরও আর্থিক লাভের একটি দিক অবশ্যই আছে। পরন্তু মানসিক তৃপ্তি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও রয়েছে। যা বাড়তি পাওনা। এর বাইরে একটি জরুরি কথা রয়েছে। শিল্প-সাহিত্যে যে দেশ ও জাতি যতটা উন্নত, তারা ততটাই সভ্য। একইসঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রগণ্য। এরমধ্যে জার্মানি, ব্রিটেন, গ্রিস, ফ্রান্স, ইরান, রাশিয়া, জাপান ও ভারতের প্রসঙ্গ সবার আগে উল্লেখ করা যায়। এসব দেশের সাহিত্য যতটা উন্নত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ততটাই উন্নত। এর কারণে সাহিত্য এসব জাতিকে সুকুমারবৃত্তির উপকরণ জুগিয়েছে। চিন্তা ও কল্পনার সীমা প্রসারিত করেছে। ফলে তাঁদের কল্পনা-চিন্তার সঙ্গে প্রজ্ঞা ও অনুসন্ধিৎসাও বেড়েছে। বিপরীতে আফগানিস্তান, উত্তর কোরিয়া, মিয়ানমারসহ পৃথিবীর বহু দেশ আছে, যে-সব দেশের সাহিত্য যত অবহেলিত, তাঁদের সভ্যতাও ততটাই পশ্চাৎপদ। তাঁরা ততটাই বর্বরতায় আচ্ছন্ন।
তথ্যসূত্র
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবন্ধ সমগ্র, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪১১
২. মোহাম্মদ নূরুল হক, বাংলা উপন্যাসে বিধবা : বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎ, বাংলানামা, ঢাকা, ২০২৩, পৃ. ৯
৩. হীরেন চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণগোপাল রায় সম্পাদিত, সাহিত্য-প্রবন্ধ: প্রবন্ধ-সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৯৯৬
৪. তদেব, পৃ. ৯৯৬
৫. আবদুল হক, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৭৬
৬. আবুল ফজল, শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৮৫